আমার মাস্টারমশাই: কবি দিনেশ দাস
স্যার বললেন, আজকে স্কুলে ঢুকে আগে টিচার্স রুমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। বুঝেছিস?
আমি খুব খুশি। স্যার টিচার্স রুমে যেতে বলেছেন মানে, এই স্যারও জানেন, ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যারেরা যেই ক্লাস থেকে বেরোতে যায়, অন্যান্য ছেলেদের মতো আমিও স্যারের কাছ থেকে চকের টুকরো নেওয়ার জন্য পিছু পিছু যাই। কোনও কোনও দিন পাই, কোনও কোনও দিন পাই না। পেলেও, ব্ল্যাকবোর্ডে অনেক কিছু লেখার জন্য কিংবা লিখতে লিখতে মাঝখান থেকে ভেঙে যাওয়ার জন্য স্যারের হাতের শেষ অংশটা এত ছোট হয়ে যায় যে, ধরে লেখার মতো অবস্থায় থাকে না।
তখন আমরা ওগুলিকে গুঁড়ো করে হাতের তালুতে নিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই এর তার মুখের সামনে আচমকা ফুঁ দিয়ে এমন করে উড়িয়ে দিই যে, সে একেবারে সাদা ভূত হয়ে যায়। কারও কারও চোখেও চলে যায়। সেটা নিয়ে কেউ কেউ আবার শুধু মনিটারকেই নয়, ক্লাস টিচারকেও নয়, সোজা হেড মাস্টারমশাইয়ের কাছে গিয়ে কেঁদেকেটে একশা করে। তখন হাতে বেতের বাড়ি খাওয়ার জন্য অথবা ক্লাসের বাইরে নিল ডাউন হয়ে বসে থাকার জন্য রেডি হয়ে থাকতে হয়। তা সত্ত্বেও পর দিন সব কিছু বেমালুম ভুলে গিয়ে আবার যে কে সেই।
তা হলে কি স্যার আজকে আমাকে একটা আস্ত চক দেবেন!
স্যার আমাদের চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে পড়ালেও উনি আমার গৃহশিক্ষকও বটে। আগে ওঁর বাড়িতে গিয়েই পড়তাম। কিন্তু পড়তে বসার খানিকক্ষণ পরেই পাশের ঘরে শুরু হয়ে যেত দক্ষযজ্ঞ। এটা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওঁর ছেলে শান্তনুদা বাবার মতো অত নামকরা না হলেও কবিতা লিখতেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপাও হত। বিয়ে করেছিলেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষিকা এবং মঞ্চাভিনেত্রী সীমন্তিনীকে। সে সময় একমাত্র ঘূর্ণীয়মান মঞ্চ সারকারিনায় ‘বারবধূ’ নাটকে উনি অভিনয় করতেন।
সে সময় শান্তনুদা প্রায়ই মদ খেয়ে গর্বের সঙ্গে বলতেন, আমার বউ এলিতেলি কারও সঙ্গে শোয় না। ওর একটা স্ট্যাটাস আছে। শুলে সমর মুখার্জির সঙ্গে শোয় কিংবা সমরেশ বসুর সঙ্গে। তার নীচে ও নামে না। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ওই নাটকের পরিচালক ছিলেন সমর মুখোপাধ্যায় আর কাহিনিকার সমরেশ বসু।
তো, শান্তনুদারা প্রেম করেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর থেকেই বউ আর শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন না। থাকতেন তাঁর বাপের বাড়ি, কেওড়াতলা মহাশ্মশানের উল্টো দিকে ৩এ, রজনী ভট্টাচার্য লেনে।
ওখানে থাকলেও প্রতিদিনই সকালের দিকে একবার করে আসতেন। আর এলেই শুরু হয়ে যেত কথা কাটাকাটি। ঝগড়া। গালাগালি। হাতাহাতি। এমনকী জিনিস ছোড়াছুড়িও। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা এমন ভয়াবহ আকার নিত যে, মনে হত এক্ষুনি বুঝি কেউ খুন হয়ে যাবে। ফলে স্যার আমাকে ছুটি দিয়ে দিতেন।
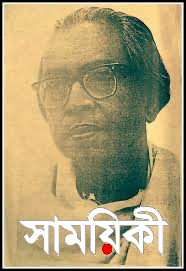
কোনও কোনও দিন উনি আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তেন। আফতাব মসজিদ লেন থেকে বেরিয়ে গোপালনগর রোড ধরে চেতলা বাজারের দিকে আসতেন। সেখানে একটা মিষ্টির দোকান ছিল। উনি জিলাপি খেতেন। আমাকেও একটা দুটো দিতেন। স্কুলের টিফিনের সময় দেখেছি, উনি প্রায়ই হজমিওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হজমি খেতেন। বনকুল খেতেন। তেঁতুলের চাটনি খেতেন।
তখন স্কুলের শিক্ষকদের মাইনে ছিল ভীষণ কম। এত কম যে মাংস খাবেন বলে তিনি একবার প্রফিডেন্ট ফান্ড থেকে লোনের আবেদন করেছিলেন। এবং কারণ হিসেবে, অন্যদের মতো ‘মেয়ের বিয়ে’ অথবা ‘বাড়ির কেউ অসুস্থ’ কিংবা ‘ঘরের চাল সারাতে হবে’র মতো কোনও অজুহাত দেখাননি। তিনি মাংস খাওয়ার কথাই লিখেছিলেন।
অগত্যা একদিন স্যার বললেন, নাঃ। তোকে আর কাল থেকে আমার বাড়িতে পড়তে আসতে হবে না। আমি তোর বাড়িতে গিয়ে পড়াব।
তা হলে কি শান্তনুদার জন্য! নাকি সে দিনের সেই ঘটনার জন্য উনি এই কথা বলছেন!
আমার মনে পড়ে গেল, দিন কতক আগে স্যারের আর এক ছেলে ভারবির জন্মদিন ছিল। সেই উপলক্ষে বাড়িতে পায়েস হয়েছিল। সবাইকেই হাতা মেপে মেপে বাটি করে দেওয়াও হয়েছিল। স্যারই বোধহয় বলেছিলেন, আমার জন্য একটু রাখতে। তাই আমি ঢোকামাত্র ভিতর-বাড়ির দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে উনি বলেছিলেন, হ্যাঁরে, ও এসেছে। ওর পায়েসটা দে।
একবার নয়। দু’বার নয়। বারকতক বলার পরে ওঁর মেয়ে বন্ধ দরজার একটা পাল্লা সরিয়ে উঁকি মেরে বলেছিলেন, আমি তো বাটি করে ওর জন্য সরিয়ে রেখেছিলাম। এখন দেখছি বাটি খালি। কেউ বোধহয় খেয়ে নিয়েছে।
শুনেই স্যারের সে কী চোটপাট। লুকিয়ে রাখতে পারিসনি? মেয়েকে এই মারেন কি সেই মারেন।
স্কুলে বাংলা পড়ালেও স্যার আমাকে সবই পড়াতেন। স্যার এলে মা তাঁকে দু’-তিনটে হাতরুটি আর বেশ খানিকটা চিনি দিতেন। প্রথম প্রথম রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিনি দিয়ে খেলেও তার ক’দিন পর থেকেই আসার সময় উনি মাখন কিনে নিয়ে আসতেন। আমাদের বাড়ির ক’হাত দূরেই একটা দোকান ছিল। কাঠের চামচে করে তুলে কলাপাতায় মুড়ে কাঠি দিয়ে আটকে দিত। যাতে খুলে না যায়। পনেরো পয়সার মাখন মানে অনেকখানি মাখন।
আমি দাওয়ায় বসে পড়তাম। গরমকালে প্রচুর রোদ পড়ত সেখানে। কিন্তু শীতকালে যে সুয্যিমামা কেন বিমুখ হতেন, জানি না। উঠোনের ও প্রান্তে এসেই থমকে যেতেন।
তখন শীতকাল। আমাকে অঙ্ক করতে দিয়ে উনি উঠোনের ওই দিকটায় গিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন। খানিক বাদে কানাউঁচু কলাইয়ের থালায় করে মা রুটি-চিনি দিয়ে গেলেন। উনি গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে যেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে কলাপাতার মোড়কটা বার করেছেন, অমনি তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। উনি খেয়ালই করেননি, কখন রোদের তাপে মাখন গলে গিয়ে পাঞ্জাবির পকেট বেয়ে পাজামার হাঁটু অবধি ভিজিয়ে দিয়েছে।
স্যার এ রকমই ছিলেন। তাই স্কুলের ছাত্ররাও অন্যান্য স্যারদের তুলনায় তাঁর পিছনে একটু বেশিই লাগত। এই শীতকালের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে আর এক শীতকালের কথা। সে বার কলকাতায় জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। স্যার ক্লাসে এসে বললেন, আজ আর এখানে নয়, ছাদে রোদ পোহাতে পোহাতে তোদের পড়াব। চল, ছাদে চল।
আমরা সবাই হইহই করতে করতে ছাদে চলে গেলাম। যদিও আমাদের স্কুলের পোশাক ছিল সাদা জামা কালো প্যান্ট। আর পায়ে কালো শ্যু। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেরই সে সব ছিল না। পায়ে চটি, কেউ কেউ স্যান্ডেল পরেও আসত।
মনে আছে, একবার পনেরো আগস্টের আগের দিন হেড মাস্টারমশাই এ ঘরে ও ঘরে ঢু মারতে মারতে আমাদের ঘরে এলেন। এসেই ক্লাসের সাতচল্লিশ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিন জনকে স্কুলের পোশাকে দেখে বাকিদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তোমরা স্কুলের ড্রেস পরে আসোনি কেন?
কেউ বলেছিল, বাবা কিনে দেয়নি স্যার। কেউ বলেছিল, নেই স্যার। আবার কেউ বলেছিল, ক্লাস ফোরে কিনেছিলাম স্যার। ছিঁড়েটিরে গেলেও মা সেলাই করে দিত। সেই ভাবে জোড়াতাপ্পি দিয়ে চার বছর পরেও ছিলাম। কিন্তু তার পর এত টাইট হয়ে গেছে যে আর পরতে পারি না। বিশ্বাস না হলে বলবেন স্যার, কাল নিয়ে আসব।
সে দিন হেড মাস্টারমশাই বলেছিলেন, শোনো, সামনে পুজো আসছে তো?
সবাই ঘাড় কাত করে বলেছিল, হ্যাঁ স্যার।
— তোমাদের বাবা তোমাদের নতুন জামাকাপড় কিনে দেবেন তো?
— হ্যাঁ স্যার, কিনে দেবে স্যার। বাবা বলেছে।
— ঠিক আছে। তা হলে একটা কাজ করো। কিনবেই যখন, তখন আর অন্য কিছু কিনো না। সাদা জামা, কালো প্যান্ট আর কালো বুট জুতো কিনে দিতে বোলো। তা হলে পুজোতেও পরতে পারবে, আবার স্কুলেও পরে আসতে পারবে। কী বললাম, বুঝেছ?
স্যারের কথা শুনে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেউই যে হেড মাস্টারমশাইয়ের কথা শোনেনি, পুজোর পরে স্কুলে গিয়েই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।
তো, স্যারের কথা মতো ছাদে গিয়ে দেখি, টেবিল চেয়ার তো দূরের কথা, একটা শতরঞ্চিও পাতা নেই। কোথায় বসব স্যার? একজন জি়জ্ঞেস করতেই, উনি বলেছিলেন, কেন? মাটিতে বস।
আমরা যে যার চটি খুলে, যাদের পায়ে বুট জুতো ছিল, তারা ব্যাগের ভিতর থেকে একটা বই বা খাতা বার করে তার উপরে বসে পড়েছিল।
স্যার পড়াতে শুরু করলেও আমাদের প্রায় কারওরই মন ছিল না পড়ায়। ছাদের গা ঘেষে মাথা তুলে দাঁড়ানো তাল গাছের মাথায় একটা কাকের বাসা ছিল। সেখানে তিনটে ছানাও ছিল। মা-কাক মাঝে মাঝেই কী যেন মুখে করে নিয়ে এসে ছানাগুলোকে খাওয়াচ্ছিল। কেউ সেটা দেখছিল। কেউ নীল আকাশে পতপত করে ওড়া ঘুড়ি দেখছিল। কেউ খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে কাগজের গোল্লা পাকিয়ে একে তাকে ছুড়ছিল। কেউ কেউ আবার মুখ দিয়ে নানা রকম উদ্ভট শব্দ করছিল।
পড়াতে পড়াতে স্যার হঠাৎ রেগে গিয়ে একজনকে ধরলেন, এই… এই… এই… তুই… তুই… তুই…
স্যার রেগে গেলে তোতলাতে শুরু করতেন। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুখ থেকে থুতু ছিটতে শুরু করত। শোনা যায়, যে বার চেতলা পার্কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন, উনি তাঁকে বরণ করেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু নেতাজি নাকি সে ভাবে কোনও কথাই বলতে পারেননি। কারণ, তিনি রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মোছায় ব্যস্ত ছিলেন।
যার বই নিয়ে উনি পড়াচ্ছিলেন, সে দূর থেকেই চিৎকার করে উঠেছিল, স্যার, বইটা ভিজে যাবে স্যার…
সঙ্গে সঙ্গে মুখের সামনে থেকে বইটা নামিয়ে উনি তাকে বলেছিলেন, আমি কি পড়াচ্ছিলাম, শুনেছিস তো?
— শুনেছি স্যার।
— শুনেছিস? আচ্ছা, একটা উদাহরণ দে তো… অধিকরণে এ বিভক্তি, কী হবে বল, বল বল বল…
ছেলেটি বলেছিল, ছাদে পাগলা স্যার…
— ছা… দে… পা… গ্… লা… হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। ঠিক… বলার সঙ্গে সঙ্গেই উনি বুঝতে পারলেন, ব্যাকরণগত ভাবে উদাহরণটা ঠিক বললেও, আসলে ছেলেটা পরক্ষ ভাবে তাঁকে পাগলা বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে চটি খুলে ছুড়ে মারলেন ওর দিকে। লাগ তো লাগ, লাগল গিয়ে তার হাঁটুতে। ছেলেটা বুক ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
— কী রে, কী হল?
স্যার কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাকি ছেলেরা হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে ওর উপরে ঝুঁকে পড়ল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। ওই ভিড় থেকেই কে যেন চিৎকার করে উঠল, স্যার, ও মনে হয় মরে গেছে।
— কী বলছিস! স্যার একেবারে বাকরুদ্ধহীন। ওর কাছে ছুটে গেলেন ঠিকই, কিন্তু বাকি ছেলেগুলিকে সরিয়ে তাঁর আর ওর সামনে যাওয়া হল না। যতক্ষণ পিরিয়ড চলছিল, আমরা হইহট্টগোল করেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।
আমি তখন রাসবিহারী মোড়ের কাছে গুরুদুয়ারার পাশে সাউথ ক্যালকাটা ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনে বক্সিং শিখি। রাজ্য মিটে যাব যাব করছি। ভূতনাথ, সিধুদারা তখন আমাদের লক্ষ্য। টানা তিন দিন ধরে প্রদর্শনী ম্যাচ। দূর-দূরান্ত থেকে খোলোয়াড়েরা আসছে। আমার যে দিন খেলা ছিল, আমি সে দিন স্যারকে যেতে বলেছিলাম।
না। পয়েন্টে নয়। আমার বিপক্ষের মুষ্ঠিযোদ্ধাকে একেবারে নক আউট করে আমি জিতেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝেছিলাম, স্যার আসেননি। এলে নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে আমাকে বাহবা দিতেন। যেমন রিং থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ক্লাবের বড়রা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলেন।
পর দিন স্যার যখন পড়াতে এলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার কালকে এলেন না?
স্যার বলেছিলেন, আঘাত করে যে জয়, সেটা আসলে জয় নয়, পরাজয়।
কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, আমি জিতেছি দেখে স্যার বুঝি খুশি হননি। মনে মনে বলেছিলাম, নিজে পারবেন না… অথচ অন্য কেউ পারলেও… কই, আপনি তো কবিতা লেখেন। আমি কি কখনও আপনাকে হিংসে করি… যেটা যে পারে, তার জন্য তাকে প্রশংসা করা উচিত।
সে দিন ছিল বুধবার। তখন রেডিয়োর যুগ। বুধবার-বুধবার যাত্রা হত। সেই রাতে যে যাত্রাটা শুনেছিলাম, তার একটা লাইন আমার বেশ ভাল লেগেছিল। লাইনটা ছিল— বিনা রণে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।
রণ মানে কী! কাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিলাম। এখন আর মনে নেই। সে-ই বলেছিল, রণ মানে যুদ্ধ। শব্দটা আমার এত ভাল লেগে গিয়েছিল যে, আমি নিজের মনেই ওই শব্দটা বারবার আওড়াচ্ছিলাম। তখনই আমার মনে হয়েছিল, উনি তো কবিতা লেখেন। তাই ওই কথা বলেছেন, না? ঠিক আছে, আমিও কবিতা লিখব। দেখিয়ে দেব। তখনই ওই ‘রণ’ নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম।
কিন্তু কবিতা লিখলেও স্যারকে দেখানো যাবে না।
কারণ, স্কুলের বাংলা বইতে এই স্যারেরই লেখা একটা কবিতা আমাদের পাঠ্য ছিল। না। তখন আমাদের মতো পরিবারগুলিতে নতুন বই কেনার চল ছিল না। কিনলেও, ক’দিন পরেই তো পুরনো হয়ে যাবে। নতুন কিনে কী লাভ! তাই যারা পাশ করে এক ক্লাস উপরে উঠে যেত, তাদের বইই হাফ দামে কেনা হত। কিন্তু বই খুলে দেখি, স্যারের কবিতাটায় ক’লাইন পরে পরেই দুটো করে লাইন নেই। ফাঁকা। আমার মনে হল, ছাপা পড়েনি। স্যার দেখলে বকবেন। বলবেন, দেখে কিনতে পারিস না?
তখন অত বুদ্ধি ছিল না যে, অন্য কোনও সহপাঠীর বই থেকে লাইনগুলো টুকে নেব। তাই যে লাইনগুলো নেই, আমিই বানিয়ে বানিয়ে ওই কবিতার সঙ্গে মানানসই করে গুঁড়ি গুঁড়ি অক্ষরে লিখে ফাঁকা জায়গাগুলি ভরাট করে নিয়েছিলাম।
অনেক দিন পরে স্যার ওই কবিতাটা পড়াতে গিয়ে আমার লেখা ওই লাইনগুলো দেখে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, এটা কী করেছিস?
— ছাপা পড়েনি স্যার। কী লেখা ছিল জানি না তো… তাই আমিই বানিয়ে বানিয়ে লিখে নিয়েছি।
আর কোনও কথা নয়। চুলের মুঠি ধরে স্যার এমন উত্তম মধ্যম দিয়েছিলেন যে, বেশ কয়েক দিন ধরে আমার গা হাত পা ব্যথা ছিল। পরে অবশ্য উনি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, ওটা ছাপার ভুল নয়, ওটাকে বলে— স্পেস।
কিন্তু আমি না বললে কী হবে, আমি যে স্যারের উপরে রেগে গিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলেছি, সে কথা আমিই ভুলে গিয়েছিলাম। ফলে খাতা থেকে ওই পাতাটা আর ছেঁড়া হয়নি। স্যার অঙ্ক করাতে করাতে পাতা ওল্টাতে গিয়ে ওটা দেখে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে লিখেছে?
আমি বলেছিলাম, এমনিই লিখেছি স্যার। ঘুম আসছিল না…
স্যার ওই কবিতাটা বার কতক পড়ে পেন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওটার ওপরে কী যেন করছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, উনি এমন ভাবে কাটছেন, আমি যাতে ওটা কখনওই আর কাউকে পড়ে শোনাতে না পারি।
যখন উঠছেন, তখন বললেন, দ্যাখ তো পড়তে পারিস কি না…
আমি দেখলাম, আমি যে কবিতাটা লিখেছিলাম সেটা কেটেছেটে, শব্দ পাল্টে, বেশ কয়েকটা ভুল বানান উনি ঠিক করে দিয়েছেন। যাবার সময় বললেন, একটা বড় কাগজে সুন্দর করে ধরে ধরে এটা কপি করে রাখিস তো…
আমি কপি করে রেখেছিলাম। পর দিন যখন এলেন, পড়ানো শুরু করার আগেই উনি বললেন, কীরে, ওটা কপি করেছিলি?
আমি বললাম, হ্যাঁ। বলেই, ওটা এগিয়ে দিলাম। দেখলাম, উনি পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। উপরে পঁচিশ পয়সার স্ট্যাম্প লাগানো। তার পর উনি আমার খাতাটা নিয়ে দু’লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি লিখে ওই কবিতাটার সঙ্গে ভাঁজ করে খামের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। জিভ দিয়ে চেটে খামের মুখটা আঁটকে দিলেন। উপরে লিখে দিলেন— সাগরময় ঘোষ, দেশ পত্রিকা, ৬ ও ৯ সুতারকিং স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩।
আমাকে বললেন, যা, এটা লেটার বাক্সে ফেলে দিয়ে আয় তো… আমাদের গলির মুখেই ছিল আমার সমান লাল রঙের একটা গোল মতো ডাকবাক্স। দিনে তিন বার করে পোস্টম্যানেরা ওখান থেকে চিঠি নিয়ে যেতেন। আমি তাতে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম।
আমি দেশ পত্রিকার নাম শুনিনি। সাগরময় ঘোষেরও নয়। ফলে উনি কাকে পাঠাচ্ছেন, কেন পাঠাচ্ছেন, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পরে দেখি, একজন সাইকেল পিওন আমাদের বাড়ির সামনে এসে আমার খোঁজ করছেন। সাইকেলের সামনের রডে বিঘতখানেক লম্বা আর হাত দেড়ের চওড়া একটা টিনের পাত ঝোলানো। তার এক দিকে লেখা আনন্দবাজার পত্রিকা। অন্য দিকে অমৃতবাজার পত্রিকা।
পিওনটা আমাকে একটা বই আর পঞ্চাশ টাকার একটা চেক দিয়ে গেলেন। পঞ্চাশ টাকা মানে অনেক টাকা। কিন্তু এটা ভাঙাব কী করে! আমার তো কোনও অ্যাকাউন্টই নেই। যে কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে কম করেও পাঁচ টাকা লাগবে।
ছুটে গেলাম স্যারের বাড়ি। বইটা হাতে নিয়ে উনি বললেন, এটা কী জানিস? এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার সব থেকে সেরা পত্রিকা। এই দ্যাখ, তোর সেই কবিতাটা ছাপা হয়েছে।
আমি দেখলাম, সত্যিই তাই।
উনি বললেন, আজকে স্কুলে ঢুকে আগে টিচার্স রুমে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি, বুঝেছিস? আর আসার সময় সঙ্গে করে এই বইটা নিয়ে আসিস।
আমার তো খুব আনন্দ। না। কবিতা ছাপা হয়েছে দেখে নয়। পঞ্চাশ টাকার চেক পেয়েছি বলে। আর তার থেকেও বড় কথা, স্যার এত খুশি হয়েছেন আর নিজের থেকেই যখন টিচার্স রুমে যেতে বলেছেন, তার মানে শুধু আজকেই নয়, আমার মনে হয়, মাঝে মাঝেই উনি আমাকে একটা করে নতুন চক দেবেন।
আমি টিচার্স রুমে ঢুকতেই দেখি, শুধু স্যারই নয়, ওই ঘরে যত শিক্ষক ছিলেন, সবাই-ই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। স্যারই আমাকে ডেকে তাঁর পাশের চেয়ারে বসতে বললেন। বুঝতে পারলাম, আমার কবিতা ছাপা হওয়ার ব্যাপারটা স্যার আগেই সবাইকে বলে দিয়েছেন।
আশেপাশে যত শিক্ষক ছিলেন, তাঁদের দেখিয়ে উনি বললেন, শোন, এখানে যারা আছে না, তারা অনেকেই কবিতা লেখে। কিন্তু আজ অবধি এদের কারও কবিতাই দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়নি। চল, হেডস্যারের ঘরে চল।
তার পর স্যার আর হেড মাস্টারমশাই আমাকে নিয়ে একতলা দোতলা তিন তলার প্রত্যেকটা ক্লাসে গেলেন। এবং আমার কবিতা যে দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তা বললেন। কোনও কোনও ক্লাসে, বিশেষ করে সিনিয়রদের ক্লাসে ঢুকে স্যার আমাকে ওই কবিতাটা পড়ে শোনাতে বললেন। আমিও শোনালাম।
আর সে দিনই, আমাদের স্কুলে টিফিনের সময়ই ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল। যখন বান আসে, টালিনালা উপচে স্কুলের স্কুলের ভিতরে জল ঢুকে যায়। তখন ছুটি হয়ে যায়। কিংবা কেওড়াতলা শ্মশানে যখন গাদার মড়া পোড়ানো হয়, গাদার মড়া মানে, যে মৃতদেহগুলি বেওয়ারিশ, কেউ নেয় না, সেগুলি বেশ কয়েকটা জমে গেলে একসঙ্গে জড়ো করে কাঠের চুল্লিতে পোড়ানো হয়। বেশির ভাগ দেহই পঁচাগলা। ফলে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়। টেকা যায় না। তখন শুধু টিফিনের সময়ই নয়, কোনও কোনও দিন অনেক আগেই ছুটি হয়ে যায়। স্কুলের বা বিখ্যাত কেউ মারা গেলেও তার অন্যথা হয় না। কিন্তু আজ তো সে রকম কিছু ঘটেনি। তা হলে ছুটি হল কেন!
তখনই জানলাম, ওই পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয়েছে দেখেই এই ছুটি। পরে জেনেছিলাম, কোনও কোনও শিক্ষক আপত্তি করলেও, মূলত আমার এই স্যারই, যিনি শুধু একজন শিক্ষকই নন, একজন কবি, যিনি কাস্তে কবি হিসেবেই অত্যন্ত জনপ্রিয়, পরে যাঁর নামে কলকাতার চেতলা অঞ্চলের একটি দীর্ঘ রাস্তা, চেতলা রোডটির নাম বদলে তাঁর নামে করা হয়েছে— কবি দিনেশ দাস সরণি, সেই দিনেশ দাসেরই হাতযশ ছিল ওই ছুটির পিছনে।




